প্রসঙ্গ সন্দেশ / PRASANGA SANDESH
₹100.00২২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে যে পত্রিকাটির পথ চলার শুরু, তা-ই পরবর্তীকালে পালটে দেয় বাংলা শিশুসাহিত্যের গতিপথকে। মাত্র দু-বছর আট মাসব্যাপী সম্পাদনা পর্বে যিনি পত্রিকাটিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন উৎকর্ষের উত্তুঙ্গ বিন্দুতে, তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সেই প্রথম প্রকাশনায় বাঙালি ছুঁয়ে নিতে পেরেছিল বিশ্বমান_শুধু মুদ্রণ প্রযুক্তি ও পারিপাট্যের দিক থেকেই নয়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্রময় পরিবেশন ও নতুন ধারার অলংকরণের সমারোহেও। সুকুমার, সুবিনয়, সত্যজিৎ-সুভাষ_সন্দেশ-এর পরবর্তী সম্পাদনা-পর্বগুলি নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও, তথ্যের অপ্রতুলতার দরুন বিস্মৃতির অতলে প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছিল উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদনা পর্ব। গত শতাব্দীর নয়ের দশকের আরম্ভে এই ‘হারিয়ে যাওয়া’ পর্ব নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হন সুস্মিতা দত্ত। এই বই সেই গবেষণারই ফসল। হারানো সূত্রগুলিকে একত্রিত করে যে দক্ষতায় লেখিকা পত্রিকাটির প্রস্তুতিপর্ব ও প্রকাশকালীন ইতিহাস পুননির্মাণ করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ বই পড়ে উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত সন্দেশ-এর বিষয়বস্তু, লেখক, ছবি, ভাষা ও পরিবেশন ছাড়াও পাঠক আলোকিত হবেন সন্দেশ পূর্ববর্তী শিশু পত্রিকাগুলির ইতিহাস সম্পর্কে।

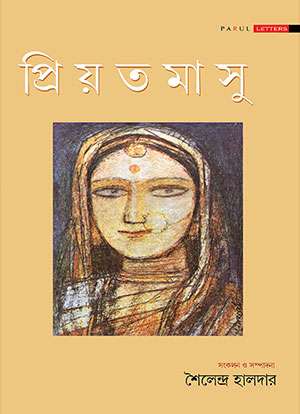
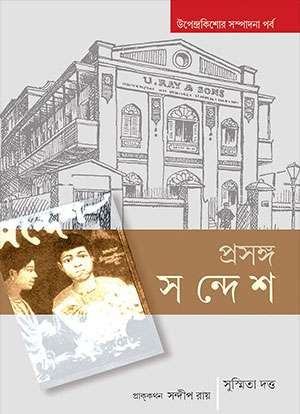
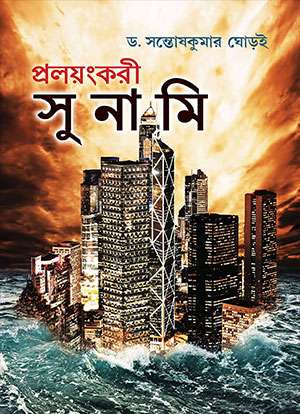
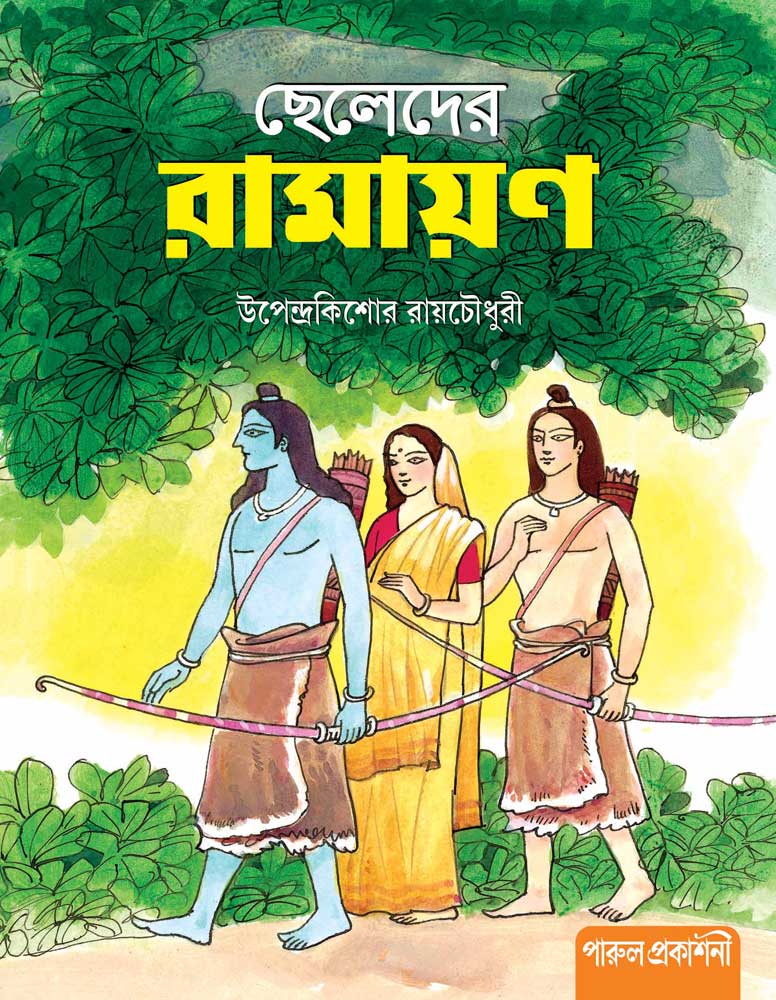
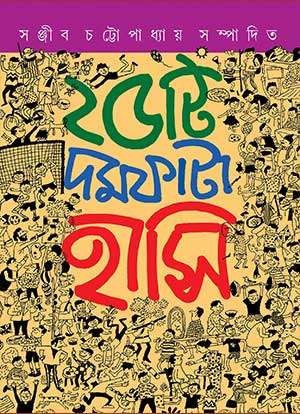
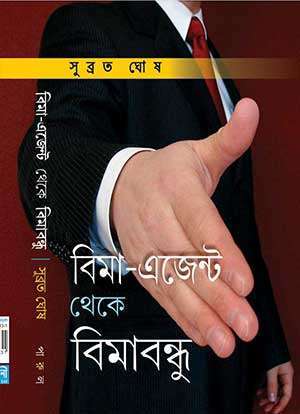
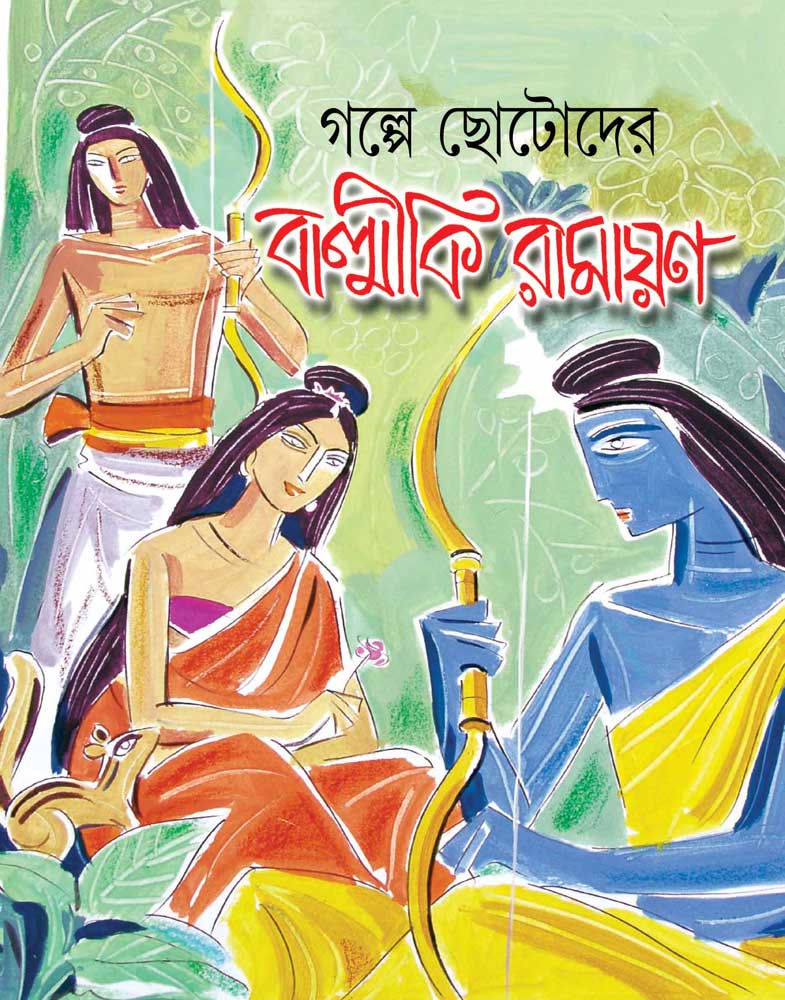
Reviews
There are no reviews yet.